জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস
আমাদের জীবন পরিবর্তনে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের অবদান অপরিসীম
ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ
৫ ফেব্রুয়ারি বুধবার জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস ২০২৫। দেশব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে দিবসটি উদযাপিত হচ্ছে। দেশের সব স্তরের মানুষকে বিশেষ করে ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষকদেরকে অধিকতর গ্রন্থাগারমুখী করে তোলা, জাতিগঠনে গ্রন্থাগারের অবদান ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা, দেশে বিদ্যমান গ্রন্থাগারগুলোতে জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার ওপর সর্বশেষ প্রকাশিত বই ও সাময়িকীর তথ্যাদি প্রদান, পাঠাভ্যাস বৃদ্ধির কলাকৌশল সম্পর্কে আলোচনা ও মতবিনিময়, মননশীল সমাজ গঠনে স্থানীয় পর্যায়ে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা, পাঠসামগ্রী সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিতরণ ও পাঠক তৈরির মাধ্যমে একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে এবং গ্রন্থাগারকর্মী ও পেশাজীবী, লেখক, প্রকাশক, পাঠক বিশেষ করে বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর অনুষ্ঠিত মন্ত্রিপরিষদের সভায় ৫ ফেব্রুয়ারিকে ‘জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস’ ঘোষণা করেন। এরপর থেকে প্রতি বছর ৫ ফেব্রুয়ারি সারা দেশে বিভিন্ন কর্মসূচির পালনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সব সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান নানা কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে উৎসবমুখর পরিবেশে দিনটি উদযাপন করে থাকে।
প্রতি বছর দিবসটির একটি প্রতিপাদ্য বিষয় থাকে। এবারকার (২০২৫) প্রতিপাদ্য হচ্ছে-সমৃদ্ধ হোক গ্রন্থাগার, এই আমাদের অঙ্গীকার’। বই জীবনের একটি প্রধান অনুষঙ্গ।একজন পাঠকের বহুমুখী রুচিবোধ থাকতে পারে। তার পাঠাভ্যাসের এই বহুমুখী রুচিবোধ নিরসনের জন্যই প্রয়োজন গ্রন্থাগার। এক ব্যক্তি যিনি বইপ্রেমী তিনি অবশ্যই তার প্রিয় বই সংগ্রহে রাখার চেষ্টা করেন এবং ব্যক্তি পর্যায়ে বাসায় কিংবা বাড়িতে ছোটখাটো গ্রন্থাগার করে বই সংগ্রহে রাখেন। কিন্তু বৃহত্তর পরিমণ্ডলে বহুমুখী জ্ঞান–বিজ্ঞান শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতির বিষয়গুলো জানতে বৃহত্তর গ্রন্থাগারের সাহায্য নিতেই হতে পারে। তাই জনগণের মধ্যে পাঠাভ্যাস সৃষ্টি এবং পাঠাভ্যাস বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে গ্রন্থাগার স্থাপন। এ লক্ষ্যে সরকারি–বেসরকারি গ্রন্থাগারগুলোর কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করা প্রয়োজন। অনেক পরিবার আছে যে পরিবারগুলি গ্রন্থাগারমুখী। যে পরিবারে গ্রন্থাগার আছে, ঐ পরিবার এক ধরনের আলাদা দ্যুতি ছড়ায় সমাজে। তাদেরকে দেখে অনেকেই উৎসাহিত হয় এবং উদ্দীপনা লাভ করে। এইভাবে সমাজ সচেতন প্রতিটি পরিবারেই যদি একটি পারিবারিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা যায় তাহলে সমাজ মননশীলতার দিকে ধাবিত হতে পারে। আর গ্রন্থাগার একটি বিদগ্ধ প্রতিষ্ঠান যেখানে পাঠক-গবেষকদের ব্যবহারের জন্য বই, পত্র-পত্রিকা, পান্ডুলিপি, সাময়িকী, জার্নাল ও অন্যান্য তথ্যসামগ্রী সংগ্রহ ও সংরক্ষিত হয়। গ্রন্থাগারের ইংরেজি প্রতিশব্দ ‘Library’-এর উৎপত্তি ল্যাটিন শব্দ Liber থেকে। যার অর্থ ‘পুস্তক’। Liber শব্দটি এসেছে Libraium শব্দ থেকে। যার অর্থ ‘পুস্তক রাখার স্থান’। এ্যাংলো-ফ্রেঞ্চ শব্দ Librarie অর্থ হলো পুস্তকের সংগ্রহ।
মুদ্রণ প্রযুক্তি আবিষ্কারের আগে বই-পুস্তক, চিঠিপত্র, দলিলাদি লেখা হতো বৃক্ষের পাতা ও বাকল, পাথর, মৃন্ময় পাত্র, পশুর চামড়া প্রভৃতির উপর। এসব উপাত্ত-উপকরণ গ্রন্থাগারে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হতো। বৈজ্ঞানিক মতে বর্তমান উন্নতির মানবজাতির ক্রমবিকাশের বয়স প্রায় ১০ হাজার বছরের। কিন্তু গ্রন্থাগারের কুষ্ঠি বিচারে বর্তমান বিশ্বে সর্বপ্রথম ৪ হাজার থেকে ৫ হাজার বছর খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে গ্রন্থাগারের উৎপত্তি হয় মিশরের সুমেরিয় অঞ্চলে ও এশিয়া মাইনারে। সম্রাট অ্যাশুরবনিপাল কর্তৃক ৬২৫ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে বিশ্বের সর্বপ্রথম প্রাতিষ্ঠানিক গ্রন্থাগার স্থাপিত হয় মিশরের নিনেভেতে। খ্রীষ্টপূর্ব ১ম শতাব্দীতে চীনে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি জাতীয় গ্রন্থাগার। সে হিসেবে বিশ্বে গ্রন্থাগার গড়ে ওঠার বয়স আড়াই হাজার বছরের। গ্রন্থাগারর সঙ্গে মানবজাতির সভ্যতা বিকাশের নিগূঢ় ও অন্তর্নিহিত বিষয় জড়িত। সভ্যতার বিকাশই হয়তো ঘটতো না যদি না প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের মধ্যে গ্রন্থাগার সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করতো। স্বীকার করতেই হবে সভ্যতার বিকাশকে ত্বরান্বিত ও যুগযুগান্তরে বিকশিত করেছে গ্রন্থাগার। বলাই বাহুল্য যে, বাংলাদেশের গ্রন্থাগার উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরার জন্য এই উপমহাদেশের সভ্যতা বিকাশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করা অপরিহার্য। প্রায় ৪ হাজার থেকে ৫ হাজার বছরের প্রাচীন ইতিহাসের ক্রমধারায় বর্ণিত গ্রন্থাগারের বিকাশ নেহায়েৎ অকিঞ্চিতকর নয়। ভারতবর্ষের গ্রন্থাগারের ইতিহাস অতি প্রাচীনকালের। গোড়া থেকেই অসংখ্য মন্দির, মসজিদ, গির্জা ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের উপাসনালয়ে ও শিক্ষিত পন্ডিত ব্যক্তিদের সংগ্রহে বিভিন্ন ধরণ ও আকারের পুঁথি কিংবা গ্রন্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল।
১. বাংলাদেশে গ্রন্থাগার উন্নয়নের সূচনা প্রায় ২ হাজার বছর পূর্বে। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে এই অঞ্চলের ময়নামতি ও মহাস্থানগড়সহ অন্যান্য বৌদ্ধ বিহারগুলোতে গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। বিশেষত বৌদ্ধ বিহারের সেসব গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত উপকরণ থেকে জ্ঞান আহরণের জন্য বিভিন্ন দূর দেশের জ্ঞান অনুসন্ধিৎসু মানুষের পদব্রজে আসা-যাওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। ৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে বাংলাদেশে গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।
২. এছাড়াও হিউয়েন সাং সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে অধিকতর অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানার্জনের জন্য এ অঞ্চলের বৌদ্ধ বিহার গ্রন্থাগারের সামগ্রী ব্যবহারের উদ্দেশ্যে আগমন করেন। উক্ত বিবরণ থেকে ভারত উপমহাদেশ তথা বাংলাদেশের গ্রন্থাগার বিকাশের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করা যায়।আর মেসোপটেমিয়া (ইরাক) অঞ্চলে প্রাপ্ত প্রায় ৩০ হাজার পোড়ামাটির ফলক নিরীক্ষা করে দেখা গেছে, এগুলি প্রায় পাঁচ হাজার বছরের পুরনো। প্রাচীন মিশরীয় নগরী আমারনা এবং থিবিস-এ প্রাপ্ত প্যাপিরাস স্ক্রলগুলি ১৩০০-১২০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দের রচনা। মেসোপটেমীয় উপত্যাকায় যথাক্রমে সুমেরীয়, ব্যাবিলনীয় এবং এ্যাসেরীয়রা বসতি গড়ে তোলে এবং সে সময়ে গ্রন্থাগার স্থাপন করে তারা সভ্যতার অগ্রগতিতে অবদান রাখে।
প্রাচীনকালে গ্রন্থাগার রাজন্যবর্গ ও অভিজাতগণ ব্যবহার করতো। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত ছিল না। সময়ের বিবর্তন, মুদ্রণযন্ত্র ও কাগজ-কালির আবিষ্কার, গ্রন্থের সহজলভ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগারের চর্চা সাধারণ্যে ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে জ্ঞানভিত্তিক সমাজে তথ্য ও গ্রন্থাগারের গুরুত্ব অনেক।
বাংলাদেশে প্রাচীনকাল থেকে পুঁথি-পান্ডুলিপি সংরক্ষণের প্রথা ছিল। এসব পুঁথি পান্ডুলিপি লিখিত হতো তালপাতায়, গাছের বাকলে বা পার্সমেন্ট, ভেলামে। উৎকীর্ণ করা হতো পাথরে অথবা পোড়ামাটির ফলকে। এগুলি সংরক্ষণ করা হতো বিভিন্ন ধর্মীয় আলয়ে বা বিহারে। বাংলাদেশে বিভিন্ন বিহারে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের বেশ কিছু পান্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া গেছে। মধ্যযুগে হোসেনশাহী রাজবংশ রাজকীয় গ্রন্থাগার স্থাপন করে। ১৭৮০ সালে শ্রীরামপুর মিশন মুদ্রিত গ্রন্থ ও পান্ডুলিপির গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করে। এর পরই কলকাতা মাদ্রাসা ও বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে পুঁথি ও মুদ্রিত গ্রন্থের সংগ্রহশালা গড়ে তোলা হয়। ১৮০১ সালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ মানবিক বিদ্যা ও বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করে। ১৮০৫ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি কলকাতায় একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করে।
১৮৫৪ সালে ৪টি গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। এগুলি হলো- বগুড়া উডবার্ন পাবলিক লাইব্রেরি, রংপুর পাবলিক লাইব্রেরি, যশোর ইনস্টিটিউট পাবলিক লাইব্রেরি এবং বরিশাল পাবলিক লাইব্রেরি। তাছাড়া রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি, ঢাকা (১৮৭১), নর্থব্রুক হল লাইব্রেরি (১৮৮২), সিরাজগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৮২), রাজশাহী সাধারণ গ্রন্থাগার (১৮৮৪), কুমিল্লা বীরচন্দ্র গণপাঠাগার (১৮৮৫), অন্নদা গোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৯০), শাহ মখদুম ইনস্টিটিউট পাবলিক লাইব্রেরি, রাজশাহী (১৮৯১), নোয়াখালী টাউন হল ও পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৯৬), উমেশচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরি, খুলনা (১৮৯৬), প্রাইজ মেমোরিয়াল লাইব্রেরি, সিলেট (১৮৯৭), ভিক্টোরিয়া পাবলিক লাইব্রেরি, নাটোর (১৯০১), চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটি পাবলিক লাইব্রেরি (১৯০৪), রামমোহন পাবলিক লাইব্রেরি, ঢাকা (১৯০৬), হরেন্দ্রনাথ পাবলিক লাইব্রেরি, মুন্সিগঞ্জ (১৯০৮)।
বিশ শতকের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পূর্ব পর্যন্ত অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে গণগ্রন্থাগার স্থাপিত হতে থাকে। এ গণগ্রন্থাগারগুলি ব্রিটিশ আমলাদের প্রশাসন চালানোর পাশাপাশি পাঠমনস্কতা, সময় কাটানো এবং মিলন কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শিক্ষিত দেশীয় ব্যক্তিদের উৎসাহে স্থানীয়ভাবে গণগ্রন্থাগারগুলি গড়ে উঠে। ১৯২৪ সালে বেলগাঁও শহরে অনুষ্ঠিত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ৩৯তম অধিবেশনে গণগ্রন্থাগার নিয়ে আলোচনা হয় এবং দেশের সর্বত্র গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হয়। একই বছর ডিসেম্বর মাসে নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনের তৃতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভায় স্থির হয়, প্রতিটি প্রদেশে গ্রন্থাগার সমিতি সংগঠন করতে হবে। ১৯২৫ সালে নিখিল বঙ্গ গ্রন্থাগার সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ডিসেম্বর মাসে কলকাতার এলবার্ট হলে গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থপ্রেমিক ব্যক্তিদের নিয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় অবিভক্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা হতে প্রতিনিধিগণ অংশ নিয়ে জেলা বোর্ড ও পৌরসভাকে গ্রন্থাগার স্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান।
পাঠদান ও একাডেমিক স্বীকৃতি প্রদান নীতিমালা–২০২২ অনুযায়ী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের লাইব্রেরির জন্য ১০০০টি, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ ও উচ্চমাধ্যমিক কলেজের লাইব্রেরির জন্য ২০০০টি বই রেখে স্বতন্ত্র লাইব্রেরি রাখা বাধ্যত্যমূলক। আর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি মোতাবেক কলেজের জন্য অবশ্যই একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার থাকতে হবে। গ্রন্থাগারে প্রতিটি বিষয়ের পাঠ্যসূচি অনুযায়ী অন্তত ৩০০০টি বই থাকতে হবে। এ বিধিতে নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও প্রয়োজনীয় রেফারেন্স বই রাখার কথাও বলা হয়েছে। কলেজ সম্মান পর্যায়ের হলে প্রতিটি বিষয়ের একটি লাইব্রেরিতে সংশ্লিষ্ট বই ও রেফারেন্স বইয়ের সংখ্যা কমপক্ষে ২০০০টি হতে হবে।বর্তমানে প্রায় প্রতিটি জেলা এবং উপজেলায় বেসরকারি গণগ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। গ্রন্থাগারের যে শ্রেণি তাতে দেখা যায় জাতীয় গ্রন্থাগার, গণগ্রন্থাগার, একাডেমিক গ্রন্থাগার, বিশেষ গ্রন্থাগার, ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার, সামাজিক গ্রন্থাগার নামের নানা গ্রন্থাগার রয়েছে। বাংলাদেশের গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের এক তথ্য অনুযায়ী জানা যায় দেশে জেলা, উপজেলা পর্যায়ে এখন মোট গণগ্রন্থাগারের সংখ্যা ৭১টি।
বাংলাদেশের জাতীয় গ্রন্থাগারে বই রয়েছে প্রায় ৫ লাখের মত। সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগারের বইয়ের সংখ্যা প্রায় ২ লাখ ৯ হাজার। ৫৮ জেলায় মোট বইয়ের সংখ্যা প্রায় ১৭ লাখ ৩৭ হাজার। এক পরিসংখ্যানে জানা যায়, সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগারে নাকি প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৩ হাজার ৩৬০ জন পাঠক আসেন। জেলা গ্রন্থাগারগুলো দৈনিক ব্যবহার করছেন গড়ে প্রায় ২ লাখ ৭৬ হাজার পাঠক। বাংলাদেশে গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে সক্ষম এ রকম শিক্ষিত জনসংখ্যার অনুপাতে গ্রন্থাগারের সংখ্যা, বইয়ের সংখ্যা এবং পাঠকের সংখ্যা নিতান্তই সামান্য। এ পরিসংখ্যার হার বাড়াতে হলে ব্যক্তি, পরিবার ও প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা থেকেই তার গোড়াপত্তন করতে হবে।
১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় থেকে এখানে একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে। বর্তমানে এ গ্রন্থাগারের গ্রন্থসংখ্যা প্রায় ৬ ল ৫০ হাজার এবং ৭৬ হাজার বাধাঁই সাময়িকী রয়েছে। এ গ্রন্থাগারে প্রায় ৩শ জার্নাল রতি আছে। দেশে ৭০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ১২ হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার রয়েছে। মাদ্রাসা কেন্দ্রিক ধর্মীয় শিা প্রতিষ্ঠানেও গ্রন্থাগার রয়েছে।
১৯২০-এর দশক থেকে গ্রন্থাগার একটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠতে শুরু করে। গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য প্রবর্তিত হয় গ্রন্থাগার শাস্ত্র।
১৯৬৫ সালে বাংলাদেশে প্রথম জাতীয় গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল শিল্প, সাহিত্য, ঐতিহ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির লালন কেন্দ্র হিসেবে কাজ করা; দেশ ও জাতি সম্পর্কে দেশিবিদেশি সকল প্রকাশনা সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণ করা; বৈধ গচ্ছিতকারী লাইব্রেরি হিসেবে কাজ করা; জাতীয় কেন্দ্র হিসেবে কাজ করা এবং সরকারের তথ্য পরিবেশন কেন্দ্র হিসেবে কাজ করা। জাতীয় গ্রন্থাগারের কার্যাবলী হলো দেশের সমস্ত পুস্তক, সরকারি প্রকাশনা ও সাময়িকী কপিরাইট আইন বলে সংগ্রহ করা এবং সংগঠন, সংরক্ষণ ও বিতরণ করা; বাংলাদেশ সম্পর্কে দেশের বাইরে প্রকাশিত পাঠোপকরণসমূহ সংগ্রহ, সংগঠন, বিন্যাস ও বিতরণ; জাতীয় গ্রন্থপঞ্জি প্রণয়ন ও প্রকাশ করা; ইউনিয়ন ক্যাটালগ প্রস্তুত করা; পান্ডুলিপি সংগ্রহ করা; আন্তঃগ্রন্থাগার সেবার সমন্বয় সাধন করা; দেশে বিদ্যমান গ্রন্থাগার সেবার সমন্বয় সাধন; আন্তর্জাতিক তথ্য বিনিময় কেন্দ্র হিসেবে কাজ করা; দেশে প্রকাশিত গ্রন্থ ও সাময়িকীর যথাক্রমে আইএসবিএন ও আইএসএসএন দেওয়া; সরকারকে তথ্য সেবা দেওয়া ইত্যাদি।
১৯৭৮ সালের ২১ জানুয়ারি ঢাকার শেরেবাংলা নগরে এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। ১৯৮৫ সালে ডাইরেক্টরেট অব আর্কাইভস অ্যান্ড লাইব্রেরিজ হিসেবে কার্যক্রম শুরু হয়। এখানে গ্রন্থপঞ্জি শাখা, গ্রন্থাগার শাখা, বাধাঁই শাখা, প্রস্ততি শাখা, কম্পিউটার শাখা, মাইক্রোফিল্ম শাখা, অনুদান শাখাসহ একাধিক শাখা রয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগারে বইয়ের সংখ্যা প্রায় ৭ লাখ। ১৯৯৬ সাল থেকে এ গ্রন্থাগার হতে আইএসবিএন দেওয়া হচ্ছে। জাতীয় গ্রন্থাগার ছাড়াও ঢাকায় জাতীয় স্বাস্থ্য গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্র নামে একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ১৯৫৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় সকলের জন্য উম্মুক্ত একটি গণগ্রন্থাগার (Public Library)। ১৯৭৭-৭৮ সালে গ্রন্থাগারটি শাহবাগের নতুন ভবনে স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত হয়। এ গ্রন্থাগার দেশের সকল জেলা উপজেলায় একটি করে গ্রন্থাগার স্থাপন করেছে।
১৯৮২ সালে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত এনাম কমিটি তৎকালীন বাংলাদেশ পরিষদকে বিলুপ্ত ঘোষণা করে। এর ফলে সরকারি গণগ্রন্থাগারসমূহ ও বিলুপ্ত বাংলাদেশ পরিষদের অধীনে জেলা ও তৎকালীন মহকুমা (বর্তমানে জেলা) পর্যায়ে পরিচালিত গ্রন্থাগারসমূহের (তথ্যকেন্দ্র) সমন্বয়ে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর গঠনের পক্ষে সুপারিশ করলে ১৯৮৪ সালে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়।
সংশ্লিষ্ট সবাই বিশ্বাস করেন, এই দিবস পালনের মাধ্যমে সব স্তরের জনগণ, ছাত্র-শিক্ষক, গবেষক সবাই বই পড়ার গুরুত্ব অনুধাবন এবং নিজেদের পাঠাভ্যাস বৃদ্ধি করে নিজ নিজ ক্ষেত্রে উন্নততর ফলাফল অর্জন করবেন এবং সার্বিকভাবে জীবনমানের উন্নতি ঘটাবেন। বলা দরকার, গ্রন্থাগার ব্যবহারের মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার এই কাজ আমরা যদি প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যাশা অনুযায়ী স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব বাস্তবায়নের এজেন্ডা মাথায় রেখে অগ্রসর হই তাহলে স্মার্ট গ্রন্থাগার স্থাপনের আর কোনো বিকল্প নেই।
সরকারিভাবে ‘জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস’ ঘোষণার ফলে দেশের সব সরকারি-বেসরকারি গ্রন্থাগার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার শিক্ষা বিভাগ, বিভিন্ন এনজিও পরিচালিত গ্রন্থাগারসহ সংশ্লিষ্ট সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি কার্যকর ও ফলপ্রসূ সমন্বয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এরূপ সমন্বয়ের ফলে দেশের গ্রন্থাগারগুলোর ব্যবহার, গ্রন্থাগার ও তথ্যসেবার মান এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।
দিবসটি ঘিরে সারা দেশের সব গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারবিষয়ক সংগঠন নানামুখী কর্মকাণ্ডে মুখর থাকে। তাতে সাধারণ মানুষ ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে গ্রন্থাগার বিষয়ে আগ্রহ ও সচেতনটা সৃষ্টি হয়েছে এবং পাঠকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্কুল এবং কলেজ পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীদের পাঠাভ্যাস বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার প্রতিদিনকার নিয়মিত শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের পাশাপাশি অত্যাবশ্যকীয় ‘লাইব্রেরি আওয়ার’ চালু করেছে। বিষয়ভিত্তিক ক্লাসের মতো প্রতিদিন ছাত্রছাত্রীরা পালাক্রমে গ্রন্থাগারে গিয়ে কমপক্ষে এক ঘণ্টা পড়াশোনা করবে। ‘জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস’ ঘোষণার ফলে দেশের সরকারি-বেসরকারি সব পর্যায়ে গ্রন্থাগার সংক্রান্ত কার্যাদি অধিকতর বেগবান হচ্ছে বলে গবেষকরা মনে করেন।
একটি জাতির মেধা ও মনন, ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির ধারক ও লালনকারী হিসেবে গ্রন্থাগার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সে জন্য বলা হয় গ্রন্থাগার হলো সমাজ উন্নয়নের বাহন। আমাদের দেশের সরকারপ্রধানরাও গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে বিভিন্ন সময় গ্রন্থাগারমুখী ব্যাপক উন্নয়ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। ঐতিহাসিকভাবে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্ব মানচিত্রে উড্ডীন হওয়ার পর বিভিন্ন সরকার কর্তৃক দেশের গ্রন্থাগার উন্নয়নের লক্ষ্যে দৃশ্যমান একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণের উদাহরণ বিদ্যমান।
এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আজ ৮ম জাতীয় গ্রন্থাগার দিবসে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে দেশের সব পর্যায়ের গ্রন্থাগার এবং শিক্ষার মান পর্যালোচনার সময় এসেছে। আমরা জানি, যে জাতির গ্রন্থাগার যত সম্মৃদ্ধ, সে জাতি তত উন্নত। আমরা এও জানি, বর্তমান যুগে কোনো জাতির উন্নয়নের ব্যারোমিটার বা পরিমাপক যন্ত্র হচ্ছে গ্রন্থাগার ও তথ্য ব্যবহারের পরিমাণ অর্থাৎ যে জাতি যত বেশি পরিমাণে গ্রন্থাগার ও তথ্য ব্যবহার করে সে জাতি তত বেশি উন্নত। গ্রন্থাগার ও তথ্য ব্যবহারের বর্তমান মানদণ্ড হচ্ছে বৈশ্বিক জ্ঞানসূচক, বৈশ্বিক অর্থনীতিসূচক এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বৈশ্বিক র্যাংকিং।
পরিশেষে বলতে চাই, আমাদের জীবনে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের অবদান অপরিসীম। গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের মাধ্যমে আমরা আমাদের জীবনের অতীত ও ইতিহাসের সম্পর্ক স্থাপন করি এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে ইঙ্গিত নির্মাণ করি। তাই গ্রন্থাগার একদিকে বহন করে কালের সাক্ষ্য, অন্যদিকে মুছে দেয় অতীত আর বর্তমানের সীমারেখা।
লেখক: কলাম লেখক ও গবেষক, প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান, জাতীয় রোগী কল্যাণ সোসাইটি।
পাঠকের মতামত:
- সুন্দরবনে ৯ দিনেও উদ্ধার হয়নি অপহৃত ১৫ জেলে
- মোংলায় আ.লীগ ও বিএনপির মধ্যে সংর্ঘষে আহত ৮
- রামপালে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের ব্যবস্থাপকের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা
- বাগেরহাটের গোয়াল ঘরে দুর্বৃত্তের আগুনে দগ্ধ ৫ গরু
- যৌনপল্লীর সুবিধাবঞ্চিত নারী ও শিশুদের জন্য ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প
- রাজবাড়ীতে বিএনপির বিক্ষোভ সমাবেশ
- ‘সৌদি, কাতার ও ওমানের প্রতিশ্রুতি আন্তরিক মনে হয়েছে’
- পাচারের অর্থ ফেরাতে কানাডার সহায়তা চাইলেন প্রধান উপদেষ্টা
- নোয়াখালীতে শিশু ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগে যুবক গ্রেপ্তার
- দিনাজপুরে দিগন্ত শিল্পী গোষ্ঠীর বার্ষিক প্রীতিভোজে বটমূলে মিলন মেলা
- পঞ্চগড় হাসপাতালে ডাক্তারের শূণপদ পূরণে অনশন, জেলা প্রশাসকের আশ্বাসে স্থগিত
- বোয়ালমারীতে স্কুলের নিরাপত্তা কর্মী আটক, মুখ খুলতে চান না পুলিশ
- মানব পাচার প্রতিরোধে সচেতনতা সভা
- একজন নারী উদ্যোক্তার গল্প
- আমাদের জীবন পরিবর্তনে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের অবদান অপরিসীম
- সাফজয়ী নারী ফুটবলারকে ধর্ষণ ও হত্যার হুমকি
- স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা দিদার হত্যা মামলায় আ. লীগ নেতা কারাগারে
- পঞ্চগড় সদর উপজেলার শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সম্পন্ন
- ‘মূল্যস্ফীতি কমাতে আরও দু-তিন মাস লাগবে’
- ‘নতুন ভোটার হচ্ছেন ৫০ লাখ’
- ‘গ্যাসের দাম বাড়ানো মরার উপর খাঁড়ার ঘা ছাড়া কিছুই নয়’
- মোস্তফা কামালের হাত ধরে সঙ্গীত জগতে এগিয়ে যাচ্ছেন এসএম মিঠু
- নড়াইল থেকে নিখোঁজ নারীর সন্ধান মিললো বাগেরহাটে
- শরীয়তপুরে সমকাল প্রতিনিধিকে হাতুড়িপেটার প্রতিবাদে মানববন্ধন
- মহম্মদপুরে রাষ্ট্র মেরামতে বিএনপির কর্মী সমাবেশ ও মতবিনিময় সভা
- দেলদুয়ার-নাগরপুরের উন্নয়নে কর্মবীর এমপি টিটু
- আওয়ামী লীগের তিনশ’ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মামলা
- ওয়ালটন জাতীয় ল্যাক্রোস প্রতিযোগিতার পুরুষ বিভাগে পুলিশ চ্যাম্পিয়ন
- মোবাইল ইন্টারনেটে ‘প্যাকেজ শর্ত’ তুলে দিলো বিটিআরসি
- প্রজন্মের কাছে এক মুক্তিযোদ্ধার খোলা চিঠি
- মঙ্গলবার থেকে ফের শুরু হচ্ছে বৃষ্টি, থাকতে পারে ৪ দিন
- ঈদগাঁওতে দিনব্যাপী শেখ রাসেল শিশু-কিশোর উৎসব
- শরীয়তপুরে বজ্রপাতে নিহত ৩
- কাঁপা
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সংকট: মুদ্রার অবমূল্যায়ন ও ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ
- শেবাচিমে সেবার মান বাড়াতে ২২ প্রস্তাব
- তীব্র শীতে ঝুঁকিতে হাঁপানী রোগীরা, প্রয়োজন জনসচেতনতা
- বাসের ধাক্কায় খাদে লেগুনা, প্রাণ গেলো ৪ জনের
- অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বীর মুক্তিযোদ্ধা কলিমুল্লাহ চৌধুরী
- ভোলার তজুমদ্দিনে আত্নরক্ষায় কারাতে প্রশিক্ষণ
- শাওমি নিয়ে এলো বহুল প্রতীক্ষিত রেডমি নোট ১৪
- পাঠ্যবইয়ে স্থান পেলেন জ্যোতি-জামাল ভূঁইয়া, বাদ সাকিব-সালাউদ্দিন
- ২০২৪ সালে চার মেধাবী শিক্ষার্থীকে হারিয়েছে ববি
- নিউ ইয়র্কে পাতাল ট্রেনে ঘুমন্ত নারীযাত্রীকে পুড়িয়ে হত্যা
- সিটি ব্যাংকের ডিএমডি হলেন মেসবাউল আসীফ সিদ্দিকী
-1.gif)
.gif)
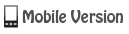






.jpg&w=60&h=50)
.jpg&w=60&h=50)
.jpg&w=60&h=50)







.jpg&w=60&h=50)

























.jpg&w=60&h=50)
.jpg&w=60&h=50)






