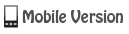বঙ্কিমচন্দ্রের পরিত্যক্ত মানস সন্তান রাজমোহন'স ওয়াইফ
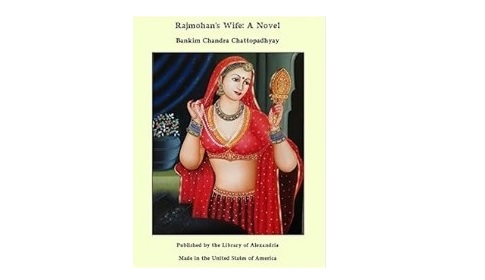
বিশ্বজিৎ বসু
বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র এবং তাঁর সৃষ্টি নিয়ে কিছু লিখতে হলে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে কোন ভূমিকা বা তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য আলাদা কোন পরিচ্ছেদ লেখার প্রয়োজন হয় বলে মনে হয়না। বঙ্কিমচন্দ্র নামটিই যেন একটি ভূমিকা। নামটি কোথাও লিখলে বা উচ্চারণ করলে মানস পটে ভেসে উঠে পাগরী মাথায় এক দীপ্তিময় মুখ। যারা তার উপন্যাস বা প্রবন্ধ পড়েছেন তাঁদের চোখে ভেসে উঠে তাঁর লেখার বর্ণনা শৈলী কিম্বা কোন দীর্ঘকায় শব্দ, আবার কারো কারো মানস পটে ভেসে উঠে তাঁর চিরায়ত বানী, 'পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ' কিম্বা 'তুমি অধম বলিয়া আমি উত্তম হইবো না কেন'।
বঙ্কিমচন্দ্র লেখালেখি শুরু করেন স্কুল জীবন থেকে। তাঁর লেখা কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৫২ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি কবিবর ঈশ্বরগুপ্তের সম্বাদ প্রভাকর পত্রিকায়। তখন বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স মাত্র তের বছর দুই মাস। এরপর থেকে পরবর্তী দুই বছর তাঁর নানা ধরনের গদ্য পদ্য রচনা প্রকাশিত হয় (রাজ মোহনের স্ত্রী, অনুবাদ: সজনিকান্ত দাস, পৃষ্ঠা ৬ )। ১৮৫৬ সালে তিনি পুস্তক আকারে প্রকাশ করেন তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'ললিতা-পুরাকালিক গল্প-তথা মানস'। যখন এ গ্রন্থ প্রকাশিত হয় তখন তিনি ছিলেন হুগলি কলেজের ছাত্র। কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে বঙ্কিম চন্দ্র পরবর্তীতে লিখেছেন, "ইহা নিরস, দুরূহ এবং বালক সুলভ অসাড় কথায় পরিপূর্ণ। উহার দুরূহতা দেখিয়া আমার একজন অধ্যাপক বলিয়াছিলেন, এগুলো হিয়ালী" (কবিতা পুস্তক, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গদর্শন যন্ত্রনালয়, ১৮৭৮, পৃষ্ঠা ১২)। ১৮৫৬ সাল হতে ১৮৬৪ সাল পর্যন্ত তাঁর লেখালেখির কোন নমুনা পাওয়া যায় না। প্রায় আট বছর পর ১৮৬৪ সালে ইন্ডিয়া ফিল্ড পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর ইংরেজি ভাষায় রচিত প্রথম উপন্যাস “রাজমোহন'স ওয়াইফ“। এটি বঙ্কিমচন্দ্র রচিত প্রথম উপন্যাসও বটে।
"মধুমতি নদীর তীরে রাধাগঞ্জ একটি ক্ষুদ্র গ্রাম হইলেও কয়েকজন বর্দ্ধিষ্ণু জমিদারের বাস আছে বলিয়া গ্রামটিতে লক্ষ্মীশ্রী আছে।" বঙ্কিমচন্দ্র এই বাক্যটি দিয়েই শুরু করেছেন তারঁ প্রথম উপন্যাসের কাহিনী। যশোর, ফরিদপুর তথা বাংলাদেশের মানুষের জন্য বিষয়টি এজন্য গর্বের যে, বঙ্কিমচন্দ্র এ উপন্যাসেরে পটভুমি হিসাবে ব্যব্হার করেছেন যশোর এবং ফরিদপুরে মাঝ দিয়ে বয়ে যাওয়া মধুমতি নদীর পাড়ের একটি গ্রামকে। রাজমোহন'স ওয়াইফ শুধু বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস নয়, এটি বাংলা তথা ভারতবর্ষের কোন লেখকের রচিত প্রথম ইংরেজি উপন্যাস। ফরিদপুর এবং যশোরবাসী আরো গর্ব করতে পারে যে, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস, ভারতবর্ষের প্রথম ইংরেজি উপন্যাস রাজমোহন'স ওয়াইফ মধুমতি নদীর পাড়ের পটভূমিকায় রচিত।
বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৫৮ সালের ৭ আগষ্ট ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে যশোরে যোগদান করেন এবং ১৮৬০ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত এখানে কর্মরত ছিলেন। এরপর তিনি বদলী হয়ে নাগোয়াতে যান। ধারণা এই যে, যশোর থাকাকালীন সমযে তিনি মধুমতি নদীর পাড়ের কোন বর্ধিষ্ণু গ্রামে কোন জমিদারীর বাড়িতে তদন্তের কাজে গিয়েছিলেন এবং সেই গ্রামের জমিদার দুই তুতো ভাইয়ের বাসভবন আর তার আশে পাশের এলাকাকে বেছে নিয়েছিলেন এ উপন্যাসের পটভুমি।
রাজমোহন'স ওয়াইফ একটি সামাজিক উপন্যাস, যার কাহিনী আবর্তিত হযেছে মাতঙ্গীনি নামে এক নারীর বীরত্বপূর্ণ কীর্তীর কথা। যাকে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের শুরুতে পাঠকদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন রাজমোহনের স্ত্রী হিসাবে। কিন্তু উপন্যাসের ভীতরে ঢুকলে এক সময় জানা যায় রাজমোহনের স্ত্রী কলিকাতার নিকটবর্তী ভাগীরথী নদীর পাড়ের এক দরিদ্র পিতার দুই কন্যার মধ্যে বড়। এই দুই কন্যা মাতঙ্গীনী আর হেমাঙ্গীনি ছিল সেই দরিদ্র পিতা গরেবর সন্তান। তাদের বাবা গর্ব করে বলতেন, মেয়েরা হচ্ছে তার সম্পদ।
অন্যদিকে উপন্যাসের নায়ক মাধব মধুমতি নদীর তীরে রাধাগঞ্জ গ্রামের জমিদার পুত্র। পিতার কোলকাতায় বসবাসের কারণে সেখানেই তার পড়াশোনা এবং বেড়ে ওঠা। সেখানেই ভাগীরথী নদীর পাড়ে এক সময়ে মাধবের সাথে পরিচয় হয় মাতঙ্গীনীর। সেখান থেকেই তাদের পুর্বরাগ, পরিচয় এবং প্রেম। কিন্তু সেই পূর্বরাগ কোন পরিণতির দিকে না গিয়ে, মাতঙ্গীনীর বিয়ে হয়ে যায় পাশ্ববর্তী গ্রামের এক শক্তিমান পুরুষ রাজমোহনের সাথে। পরবর্তিতে মাতঙ্গীনীর উদ্যোগে ছোট বোন হেমাঙ্গীনিকে বিয়ে করে মাধব এবং কাকার জমিদারির উত্তরসূরী হয়ে কোলকাতা থেকে ফিরে আসে বসবাস করতে থাকে রাধাগঞ্জে।
একসময়ে হেমাঙ্গীনীর অনুরোধে মাধব রাজমোহনকে তার মহালের একটি গ্রাম দেখাশোনার দায়িত্ব দেয় এবং রাধাগঞ্জে একটি বাড়ি করে দেয়। এই বাড়িতেই স্ত্রী, দুই পুত্র, এক বিধবা পিসি আর স্বামী পরিত্যাক্তা বোনকে নিয়ে বসবাস করতে থাকে রাজমোহন।
উপন্যাসের খল চরিত্র মাধবের তুতো ভাই মথুর। মাতঙ্গীনির অঙ্গসৌষ্ঠব দেখে তার লালসার চোখ পড়ে মাতঙ্গীনীর উপর। সে মাতঙ্গীনিকে ভোগ করার ফন্দি আটতে থাকে। পাশাপাশি সে মাধবের জমিদারিকে নিজের হস্তগত করার লক্ষ্যে মাধবের নামে তার কাকিমাকে দিয়ে জলিয়াতির মামলা করায় এবং এক ডাকাতেকে নিয়োগ করে মাধবের জমিদারির উইল ছিনিয়ে আনতে। ডাকাতরা রাজমোহনকে সংগী করে সেই উইল চুরি করতে।
এক ঝড়বৃষ্টির রাতে ডাকাত দল আসে ডাকাতি করতে এবং রাজমোহনের ঘরের পিছনে বসে উইল ডাকাতির ষড়যন্ত্র করতে থাকে। মাতঙ্গীনী ডাকাতের সংগে রাজমোহনের শলা পরামর্শ শুনে ঝড় বৃষ্টির রাতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সেই খবর পৌঁছে দেয় মাধবের কাছে, রক্ষা করে মাধব এবং তার বোনকে। রাজমোহন এবং ডাকাতদল একসময় টের পায় যে, মাতঙ্গীনীই ডাকাতির খবর পৌঁছে দিয়েছে মাধবের কাছে। ফলে মাতঙ্গীনীর জীবনে নেমে আসে দূর্বিসহ যন্ত্রণা। রাজমোহন ও ডাকাতেরা মাতঙ্গীনীকে হত্যা করার উদ্যোগ নেয়। মাতঙ্গীনী পালিয়ে প্রথমে আশ্রয় নেয় মথুরের বাড়িতে এবং পরে সেখান থেকে ফিরে আসার পথে হারিয়ে যায়।
ডাকাতি ব্যর্থ হলেও ডাকাতেরাও থেমে থাকে না। একরাতে তারা অপহরণ করে মাধবকে এবং বন্ধী করে মথুরের গোপন কারাগারে। এখানেও পরোক্ষভাবে মাতঙ্গীনির সহায়তায় কারাগার থেকে মুক্তি পায় মাধব এবং মুক্তির পর মথুরের দ্বিতীয় স্ত্রী তারার সহায়তা নিয়ে আবিস্কার করে মৃত্যমুখোযাত্রী মাতঙ্গীনীকে। উদ্ধারের পর মাতঙ্গীনীর মুখ থেকে জানা যায়, মথুর গ্রামের এক মহিলার সাহয্যে নিয়ে মাতঙ্গীনী আটকে রেখেছিল কারাগারের ভীতরে তৈরি এই প্রমোদ কক্ষে এবং মাতঙ্গীনিকে অংকশায়ীনী হতে রাজি করানোর জন্য বন্ধ করে রেখেছিল খাবার।
এ ঘটনায় ডাকাত দলের একজন গ্রেফতার হয়, সে মেজিস্ট্রেটের কাছে সব কিছু স্বীকার করে। রাজমোহনও গ্রেফতার হয়, গ্রেফতার এড়াতে মথুর আত্মহত্যা করে। মামলা শেষে এক ডাকাতে সাথে রাজমোহনের দ্বীপান্তর সাজা হয়। মাতঙ্গীনীকে ফিরে যেতে হয় বাবার কাছে।
রাজমোহন'স ওয়াইফ উপন্যাসের কাহিনী একদিকে যেমন এডভেঞ্চারে পূর্ণ, তেমনই এটি বই আকারে প্রকাশিত হবার ইতিহাসও এডভেঞ্চারে পরিপূর্ণ।
বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম জীবনীকার তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শশীচচন্দ্র বঙ্কিম জীবনীতে উল্লেখ করেছেন কবিবর ঈশ্বরগুপ্তের নির্দেশনাতেই বঙ্কিমচন্দ্র গদ্য লেখা শুরু করেন। জীবনীর ভূমিকায় লিখেছেন," রাজমোহন'স ওয়াইফ নামে একটি গল্প ১৮৬২ সালে তিনি লিখিয়াছিলেন। ইহা ইংরেজি ভাষায় লিখিত হইয়াছিল এবং ইন্ডিয়া ফিল্ড নামক পত্রে তাহা প্রকাশিত হইয়াছিল। গল্পটি সম্পূর্ণ হয় নাই; সুতরাং তাহার মুল্য বেশি আছে বলিয়া বোধ হয় না। তবু আমি উক্ত পত্রের জন্য নানা দিকে সন্ধান করিয়াছিলাম। কিন্তু বাঙ্গালা দেশে কোথাও তাহা পাই নাই। অবশেষে বিলাতে পত্র লিখিয়াছিলাম। বৃটিশ মিউজিয়ামের কর্তা ফোরট্সকিউ সাহেব উত্তরে জানাইয়াছেন, ইন্ডিয়া ফিল্ডের কয়েক সংখ্যা মাত্র তথায় আছে কিন্তু উক্ত গল্প যে সংখ্যায় থাকা সম্ভব, সেই সংখ্যা পাওয়া যায় নাই।" (বঙ্কিম জীবনী চতুর্থ সংস্করণ, লেখক: শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদনা -অলোক রায়, অশোক উপাধ্যায়, পৃষ্ঠা-তেইশ)।
শচীশচন্দ্র লিখেছেন, "এ সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা ভাষার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেন। বঙ্কিমচন্দ্র উপলব্ধি করলেন, পৃথিবীর কোন লেখক মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করে প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। কোন সাহিত্যিকের বিদেশী ভাষায় বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর ইংরেজি লেখা স্থায়ী হবে না। বঙ্কিম চন্দ্র ঐসময়ে Adventure of young Hindu নামেও একখানা গল্প লিখিয়াছিলেন। তিনি সেটা লেখাও বন্ধ করে দেন। তিনি দুর্গেশনন্দিনী লেখা শুরু করেন।"
শচীশচন্দ্র বঙ্কিমের জীবনী রচনা শুরু করেন ১৩২২ সনে, বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর বাইশ বছর পর। তখনও হয়তো তিনি এই গ্রন্থের ঐতিহাসিক গুরুত্ব উপলব্দী করতে পারেন নাই বা খুঁজে না পাওয়ার বেদনা লাঘবের জন্যে মন্তুব্য করেছিলেন, "তাহার মুল্য বেশি আছে বলে বোধ হয় না।" হয়তো মাতৃভায়ার প্রতি প্রবল টানে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও এই ইংরেজি উপন্যাসকে গ্রন্থ আকারে প্রকাশ করার উদ্যেগ না নিয়ে পরিত্যাগ করেছিলেন।
দীর্ঘকাল পর্যন্ত এটাই বিশ্বাস ছিল রাজমোহন'স ওয়াইফ বঙ্কিমচন্দ্রের হারিয়ে যাওয়া অসমাপ্ত ইংরেজি উপন্যাস। কিন্তু হঠাৎ করেই একদিন অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে উদ্ধার হয় উপন্যাসটি, যেন এ উপন্যাসে হারিয়ে যাওয়া মাতঙ্গীনিকে উদ্ধারের মতো, অলৌকিক শব্দের সু্ত্র খুঁজতে গিয়ে, মাতঙ্গীনিকে খুঁজে পাওয়ার মতো।
প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ও গবেষক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গবেষণার কাজে হিন্দু পেট্রিয়টের পুরানো বাঁধাই ফাইল নিয়ে কাজ করছিলেন। একাজে তাকে সহযোগিতা করছিলেন ইতিহাসবিদ স্যার যদুনাথ সরকার এবং হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক কৃষ্টদাস পালের নাতি সীতানাথ পাল। তিনি যখন ১৮৬৪ সালের হিন্দু পেট্রিয়টের বাঁধাই ফাইলটি নিয়ে কাজ করছিলেন, তখন তিনি আবিস্কার করেন হিন্দু পেট্রিয়টের ভিতরে ইন্ডিয়া ফিল্ডের কিছু সংখ্যা বাঁধাই করা। পুস্তক বাঁধাইকারীরা ভুলক্রমে হিন্দু পেট্রিয়টের বদলে সেখানে ইন্ডিয়া ফিল্ড বাঁধাই করে রেখেছে। এবং আশ্চর্যজনক ভাবে তিনি দেখেন, যে সংখ্যাগুলোতে রাজমোহন'স ওয়াইফ ছাপা হয়েছিল, প্রথম তিনটি সংখ্যা বাদে সবগুলো সংখ্যা এখানে বাঁধাইকৃত রয়েছে। তিনি আরো আবিষ্কার করেন, বঙ্কিমচন্দ্র লেখা শেষ করেন নাই বলে শচীশচন্দ্র যে তথ্য দিয়েছিলেন, সেটা সঠিক নয়। ইন্ডিয়া ফিল্ডে পুরো উপন্যাসটিই ছাপা হয়েছে।
অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী রচনাকালে শচীশচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের ঘর হতে একটি অসমাপ্ত উপন্যাসের পান্ডুলিপি উদ্ধার করেন এবং পান্ডুলিপিটি তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ উপন্যাস হিসাবে কল্পনা করেন। এর সাথে নিজের কল্পনা যোগ করে উপন্যাসটি সমাপ্ত করেন এবং ১৩২৫ সনে 'বারি বাহিনী' নামে প্রকাশ করেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক রাজমোহন'স ওয়াইফ উদ্ধার হবার পর দেখা যায় উদ্ধারকৃত পান্ডুলীপিটি এই উপন্যাসের সপ্তম পরিচ্ছেদের প্রায় শেষ পর্যন্ত বঙ্গানুবাদ। যদিও এই উদ্ধার হওয়া অসমাপ্ত উপন্যাসের প্রথম পর্বেই রাজমোহনের স্ত্রীর কথা উল্লেখ আছে, তবুও শচীশচন্দ্র কেন বুঝতে পারেন নাই রাজমোহনস ওয়াইফ এর বঙ্গানুবাদ সেটা অজানাই রয়ে গেছে।
উদ্ধারকৃত এই সাত পরিচ্ছেদ শুধু অনুবাদ হিসাব বাংলা গদ্য সাহিত্যের সুচনালগ্নের একটি ক্ষুদ্র গবেষনাপত্রও বলা যেতে পারে। শচিশচন্দ্র বারি বাহিনীর ভুমিকায় লিখেছেন, 'বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সাধারণ ভাষা পরিত্যাগ করিয়া এক অভিনব ভাষায় এই পুস্তকখানির রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন'। এ প্রসঙ্গে সজনিকান্ত দাস তাঁর অনুদিত রাজমোহনের স্ত্রীর মুখবন্ধে লেখেন, 'আসলে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রভাববজ্জিত ভাবে এই কয়টি পৃষ্ঠাই বঙ্কিম চন্দ্রের প্রথম গদ্য রচনা। রাজমোহনের স্ত্রী অনুবাদ করতে বসিয়া বঙ্কিমচন্দ্র সেই ভাষাকে নির্ম্মমভাবে ত্যাগ করতে চেষ্টা করিয়াছেন। বিদ্যসাগর রীতি এবং আলালী রীতির পার্থক্য তিনি ধরিতে পারিয়াছেন এবং নিজের অসাধারণ প্রতিভা বলে বুঝিয়াছেন যে, এই দুই রীতির সমন্বয় ব্যতিত বাংলা ভাষার উন্নতি সম্ভব নহে। তিনিই এই দুই রীতির সমন্বয় সাধনে সচেস্ট হলেন। রাজমোহনের স্ত্রী তৎকৃত অনুবাদে এই দুই রীতির দ্বন্ধ স্পস্ট।' তিনি ভুমিকার উপসংহারে লেখেন,' “প্রাচীন ও নবীন রীতির এই দ্বন্ধের মধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য জীবনের আদি পর্বের সমাপ্তী এবং যথার্থ বঙ্কিম-প্রতিভার অভ্যুদয়। দুর্গেশনন্দিনীতে সার্থকভাবে এই ভাষা সমন্বয়ের সুত্রপাত দেখতে পাই”। রাজমোহনস্ ওযাইফ উপন্যাসের সাহিত্যিক মান বা গুরুত্ব যাই হোক না কেন, এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপিরীসীম। আর সেটাকে বিবেচনায় নিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপ্যাধ্যায় এটিকে গ্রন্থ আকারে প্রকাশ করার উদ্যোগ নেন। যেহেতু প্রথম তিন অধ্যায় উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই, সেহেতু তিনি বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক অনুবাদকৃত প্রথম তিন অধ্যায়ের ইংরেজি অনুবাদ করে ১৯৩৫ সনে বইটি সম্পূর্ণ আকারে প্রকাশ করেন। এরপর শ্রী সজনি কান্ত দাস চতুর্থ অধ্যায় হতে এর বঙ্গানুবাদ করেন এবং যা বাংলা ১৩৩৫ সন হতে বঙ্গশ্রী পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। ১৩৫১ সালে এই বঙ্গানুবাদ গ্রন্থ আকারে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের প্রথম তিন অধ্যায় তিনি যুক্ত করেন বঙ্কিমচন্দ্রকৃত অনুবাদ যা বারি বাহিনী হতে নেয়া।
ভুলও কখনও কখনও বড় বড় আবিস্কারে পথ প্রদর্শক।এরকম অনেক উদাহরণ এই পৃথিবীতে আছে। রাজমোহনস্ ওযাইফও সে রকম একটি আবিস্কার। পুস্তক বাঁধাইকারীদের একটি বড় ভুলের কারণেই আজ আমরা পেয়েছি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস তথা বাংলা ভারতের কোন লেখকের রচিত প্রথম ইংরেজি উপন্যাস। সময় যত সমানের দিকে প্রবহিত হবে এ উপন্যাসের এর ঐতিহাসিক গুরুত্বও তত বৃদ্ধি পাবে। কারণ এটি বাংলা তথা ভারতবর্ষের কোন লেখকের লেখা প্রথম ইংরেজি উপন্যাস এবং যে গ্রন্থকে বঙ্কিমচন্দ্র পরিত্যাগ করেছিলেন, এখন সেই গ্রন্থের তিনটি ভার্সন পাওয়া যায, একটি মুল ইংরেজিতে লেখা, একটি এর বঙ্গানুবাদ, আরেকটি বারি বাহিনী নামে। অন্তর্জালে খোঁজ দিলে দেখা যায় বাংলাদেশ, ভারতের বাইরে আমেরিকা থেকেও প্রকাশিত হয়েছে রাজমোহনস্ ওয়াইফ। প্রকাশ করেছে লাইব্রেরি অফ আলেক্সজান্দ্রিয়া।
লেখক : অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী।
পাঠকের মতামত:
- আয় করমুক্ত থাকবে সর্বজনীন পেনশন স্কিম
- মুক্তিযোদ্ধাদের বিড়ম্বনাময় জীবনের কথকতা
- ১ জুলাই ব্যাংক হলিডে, সব লেনদেন বন্ধ
- প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে বাইডেন ‘অযোগ্য’, আসছেন মিশেল ওবামা!
- মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বে অর্জিত দেশকে ব্যর্থ হতে দেয়া যায় না
- সুদিপা-তারিন-মাছরাঙ্গা টিভি ভনিতা না করে ক্ষমা চান
- ‘যে মানুষ বারবার পোড়ে, তার কাছে দাবানলও নত’
- দুর্নীতি রুখি
- সাবেক-বর্তমান চেয়ারম্যানের দ্বন্দ্ব, বাড়িঘর ভাঙচুর, লুটপাট
- শৈলকুপায় অবৈধ চায়না দুয়ারি জাল ধ্বংস
- ইউক্রেনজুড়ে রাশিয়ার হামলায় শিশুসহ নিহত ১২
- ১১৪ শিক্ষার্থী পেল গোপালগঞ্জ জেলা পরিষদের শিক্ষাবৃত্তি
- সোমবার থেকে সর্বাত্মক কর্মবিরতিতে যাচ্ছেন ৩৫ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা
- নতুন অর্থবছরের বাজেট পাস
- ‘দণ্ডপ্রাপ্ত খালেদার মুক্তি দাবি ধৃষ্টতা ছাড়া কিছু নয়’
- ‘গত ছয় মাসে ৯৯ হাজার শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে’
- ‘প্রতিটি উপজেলায় বড় কবরস্থান নির্মাণ করা হবে’
- এইচএসসি পরীক্ষার দিনে বৃষ্টি হলে সময় বাড়ানোর নির্দেশ
- ‘আলী যাকের মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপাঠ’র পুরস্কার পেলেন ৩০ শিক্ষার্থী
- কুষ্টিয়ায় বাড়ছে সাংবাদিক নির্যাতন
- ‘খেলোয়াড় হিসেবে জিততে পারিনি, তবে সেরা চেষ্টা করেছি’
- ‘আদালতে ৪১ লাখ মামলার জট’
- ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেট পাস আজ
- বিশ্বব্যাংকের অর্থায়ন পেয়েছে ‘জেবিআরএটিআরসি’
- ১০৯ বারের মতো পেছালো সাগর-রুনি হত্যা মামলার প্রতিবেদন
- অ্যাডভোকেট মাহাবুব উল আলমের ‘দেওয়ানী মামলার খুটিনাটি’ বইয়ের মোড়ক উন্মোচন
- প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে গৃহবধূর শ্লীলতাহানির অভিযোগ
- রায়পুরে গণধর্ষনের শিকার গৃহবধুকে স্বামীর তালাক!
- শিশুসাহিত্যিক খালেক বিন জয়েনউদদীন আর নেই
- ফরিদপুর পৌরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ড নাগরিক কমিটির সভা
- হাইকোর্টে জামিন পেয়েও বাদীপক্ষের ভয়ে বাড়ি ফিরতে পারছে না মঙ্গলহাটা গ্রামের তিন শতাধিক মানুষ
- ইরানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন আজ
- মাগুরার শিশু শিল্পী পার্বণ দে’র কন্ঠে সুরের জাদু
- পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ জেনারেল হামিদ নাটোর সফর করেন
- জেনে নিন কে এই 'প্রিন্স ড. মুসা বিন শমসের' !
- জেনে নিন কে এই 'প্রিন্স ড. মুসা বিন শমসের' !
- ‘আ.লীগের প্রতিটি কর্মী স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে কাজ করে যাবে’
- টানা ৮ দিন অতি ভারী বর্ষণের আভাস, ৩ নম্বর সংকেত
- আনার হত্যা: ৬ দিনের রিমান্ডে ফয়সাল-মোস্তাফিজুর
- অভিযোগ গঠন বাতিলে ড. ইউনূসের মামলার ২ আসামির আবেদন
- ফরিদপুরে পুরুষের চেয়ে নারী বেশি
- মহম্মদপুরে মধুমতি নদী থেকে গলিত লাশের অংশ উদ্ধার
- বঙ্গবন্ধু ডক্টরাল ফেলোশিপ প্রোগ্রাম চালু করবে ঢাবি
- ডিএমপির মাদকবিরোধী অভিযানে গ্রেপ্তার ২৮
- রাতারাতি বিএনপি নেতৃত্বে তোলপাড়: আন্দোলনে ব্যর্থতার দায় নাকি অন্য কিছু?
৩০ জুন ২০২৪
- মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বে অর্জিত দেশকে ব্যর্থ হতে দেয়া যায় না
- ‘যে মানুষ বারবার পোড়ে, তার কাছে দাবানলও নত’
-1.gif)